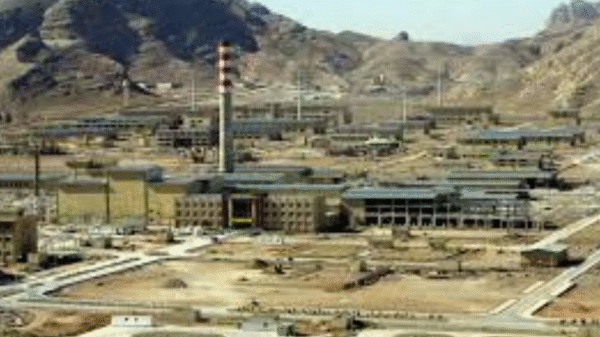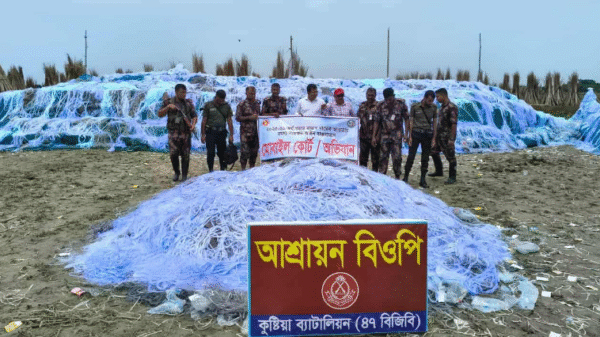হানিট্র্যাপ: গুপ্তচরবৃত্তির মধুর ফাঁদ
- সর্বশেষ আপডেট : শুক্রবার, ৮ আগস্ট, ২০২৫
- ১৮৯ জন খবরটি পড়েছেন

ভূমিকা
“হানিট্র্যাপ” — নাম শুনলেই মনে হয় রোমান্টিক কোনো ফাঁদ। বাস্তবে এটি একটি প্রাচীন কিন্তু কার্যকর কৌশল, যা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি, তথ্য চুরি, ব্ল্যাকমেইল কিংবা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য। এই কৌশলে প্রেম, যৌন আকর্ষণ বা আবেগকে হাতিয়ার করে টার্গেটকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলা হয়।
হানিট্র্যাপের সংজ্ঞা
হানিট্র্যাপ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কোনো ব্যক্তি (সাধারণত গুপ্তচর বা প্রতারক) রোমান্টিক বা যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তিকে প্রলুব্ধ করে এবং পরবর্তীতে তার কাছ থেকে গোপন তথ্য, অর্থ, বা অন্য কোনো সুবিধা আদায় করে নেয়।
এটি গুপ্তচরবৃত্তি, কর্পোরেট জালিয়াতি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং সাইবার অপরাধে বহুল ব্যবহৃত।
ইতিহাস ও উৎপত্তি
১। প্রাচীনকাল থেকে রাজনীতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে নারীর সৌন্দর্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের উদাহরণ রয়েছে। ২। রোমান সাম্রাজ্যে এবং মধ্যযুগীয় রাজকীয় দরবারে শত্রু সেনাপতি বা কূটনীতিকদের প্রলুব্ধ করে তথ্য আদায়ের নথি পাওয়া যায়। ৩। শীতল যুদ্ধের সময় (Cold War) সোভিয়েত কেজিবি ও পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিয়মিত হানিট্র্যাপ ব্যবহার করত। ৪। ডিজিটাল যুগে এই কৌশল ভার্চুয়াল ফাঁদে রূপ নিয়েছে, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া, ডেটিং অ্যাপ, ভিডিও কল ব্যবহার করে প্রতারণা চালানো হয়।
প্রচলিত কৌশল
১। শারীরিক উপস্থিতি – বার, হোটেল, কূটনৈতিক অনুষ্ঠান বা ব্যক্তিগত পরিবেশে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক গড়ে তোলা। ২। অনলাইন প্রলোভন – ভুয়া প্রোফাইল তৈরি করে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ শুরু করা। ৩। আবেগীয় সংযোগ – টার্গেটের একাকীত্ব, দুর্বলতা বা অভ্যাসকে কাজে লাগানো। ৪। ব্ল্যাকমেইল ও তথ্য চুরি – ছবি, ভিডিও বা গোপন আলাপ রেকর্ড করে হুমকি দেওয়া।
বিখ্যাত হানিট্র্যাপ ঘটনা
- মাতা হারি (Mata Hari) – প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নেদারল্যান্ডসের নৃত্যশিল্পী ও কোর্টিজান মাতা হারি ফরাসি ও জার্মান উভয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে।
- কেজিবির “সোয়ালো” অপারেশন
- শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত কেজিবি নারী ও পুরুষ এজেন্ট ব্যবহার করে পশ্চিমা কূটনীতিকদের কাছ থেকে তথ্য আদায় করত।
- ডিজিটাল হানিট্র্যাপ: ভারতের সাম্প্রতিক উদাহরণ
- ২০১৯ সালে রাজস্থানের বিমানবাহিনীর এক কর্মকর্তা ফেসবুক মেসেঞ্জারের মাধ্যমে এক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলেন, পরে জানা যায় নারীটি পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর হয়ে কাজ করছিলেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য ফাঁস করেন।
- চীনা গুপ্তচর ফাং ফাং কেস (Fang Fang)
- যুক্তরাষ্ট্রে চীনা এজেন্ট ফাং ফাং কয়েকজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে গোপন তথ্য সংগ্রহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন (২০১১-২০১৫)।
হানিট্র্যাপের ঝুঁকি ও প্রভাব
১। জাতীয় নিরাপত্তা: কূটনীতিক, সামরিক কর্মকর্তা বা বিজ্ঞানীরা আক্রান্ত হলে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ফাঁস হয়। ২। কর্পোরেট ক্ষতি: ব্যবসায়িক গোপন পরিকল্পনা বা প্রযুক্তি চুরি হতে পারে। ৩। ব্যক্তিগত জীবনে ধ্বংস: মানহানি, সামাজিক অবস্থান হারানো, আইনি জটিলতায় পড়া।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
১। অজানা ব্যক্তির সঙ্গে অনলাইনে বা সরাসরি ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করা। ২। সরকারি বা গোপন দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের নিয়মিত সাইবার সিকিউরিটি ট্রেনিং নেওয়া। ৩। সন্দেহজনক যোগাযোগ ঘটলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানো।
উপসংহার
হানিট্র্যাপ শুধু সিনেমার গল্প নয়; এটি বাস্তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, ব্যবসা, এমনকি ব্যক্তিগত জীবন ধ্বংস করে দিতে সক্ষম এক নীরব অস্ত্র। ডিজিটাল যুগে এর ঝুঁকি আরও বেড়েছে, তাই সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণই হতে পারে এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।