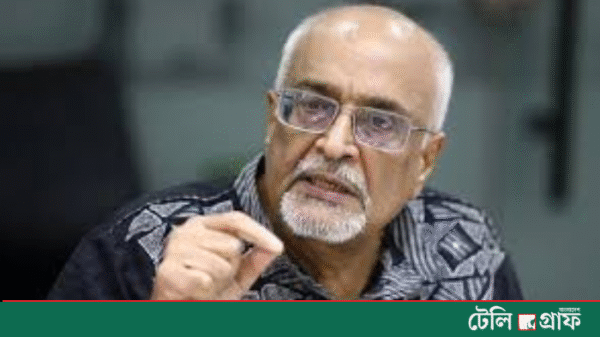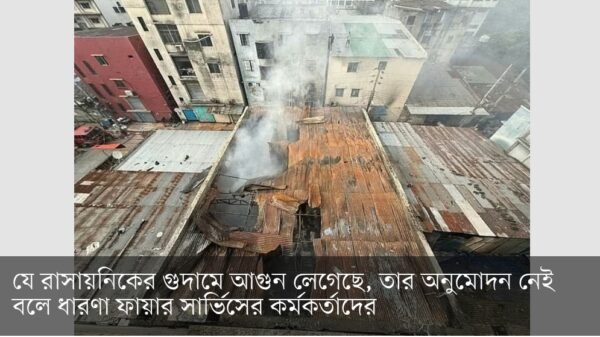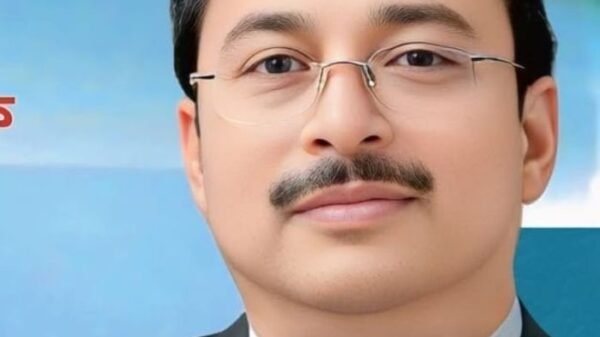রবীন্দ্রনাথ,ইসলাম ও বিদ্বেষ: একটি পর্যালোচনা
- সর্বশেষ আপডেট : শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
- ২০৮ জন খবরটি পড়েছেন

আজ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মদিন
তর্কপ্রিয় বাঙালির আমোদের বিষয় রবীন্দ্রনাথ। না, উনি কি লিখেছেন তা নিয়ে নয়, আমাদের সবচেয়ে বেশি আমোদ হয় উনি কি লিখেননি- তা নিয়ে। উগ্রপন্থী তো বটেই, বহু বামপন্থীকেও দেখেছি এই কথা বলতে যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নাকি ইসলাম নাই, রবীন্দ্রনাথের গল্পে, কাব্যে, গানে নাকি কোন মুসলমান চরিত্র নাই।
আজকের এই লেখার উদ্দেশ্যে সাদা চোখে একটু গাঢ় করে খোঁজ করে দেখা- আসলেই কি বিষয়টা এমন কি-না?
আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেশ্বরবাদী নিরাকার ব্রাহ্মধর্মের অনুসারী। এই ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে আলাদা একটা আলাপ আমরা অন্য কোন একদিন করবো। কারণ যতোই আমরা একেশ্বরবাদী, নিরাকারের কথা বলি বাঙালী মুসলমানের পেটে এই সন্দেহ বলবৎ থাকে যেহেতু ব্রাহ্মণ শব্দের সাথে ব্রাহ্ম শব্দের মিল আছে সেহেতু এই গোটা বিষয়টা আসলে কোটআনকোট হিন্দুয়ানী কিছু একটাই হবে।
সে যাই হোক, চলেন এই গরমে আমরা একটু শান্তিনিকেতন থেকে ঘুরে আসি।
রবির জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনের উপাসনা কক্ষে সকল ধর্মগুরুদের জীবন-কর্ম নিয়ে আলোচনা হতো। তাঁদের জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো গান গেয়ে।
এখনো এই প্রচলন বলবৎ আছে বলেই জানি।
উল্লেখযোগ্য চারটা গানের কথা উল্লেখ করা যায়:
১) গৌতম বুদ্ধকে স্মরণ করে গাওয়া হতো ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’
২) যিশুকে স্মরণ করে ‘এতদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে’
৩) শিখ ধর্মগুরু নানকের জন্মদিনে শোনা যেতো, ‘গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে’
৪) নবীজী হযরত মুহম্মদ( সাঃ) এর জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ করে গাওয়া হতো ‘কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো’
নবীজী কে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের উপাসনা কক্ষে গাওয়া এই গানের পুরো লিরিকটা এমন:
কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ / জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস।
এই অকুল সংসারে/ দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোরবিপদ-মাঝে/ কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে/ সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে/ কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।
তোমার ভাবনা কিছু নাই– কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে, কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।
নবীজী হজরত মুহাম্মদ ( সাঃ)কে নিয়ে কবিগুরুর অনেকগুলো লেখার খবর জানা যায়। এমন একটি লেখা ১৯৩৩ সালের ‘পয়গম্বর দিবস’-এর অনুষ্ঠানে পাঠ করেছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় যোদ্ধা সরোজিনী নাইডু। লেখাটার কিছু অংশ এমন:
‘জগতে যে সামান্য কয়েকটি মহান ধর্ম আছে, ইসলাম তাদেরই অন্যতম। মহান এই ধর্মমতের অনুগামীদের দায়িত্বও তাই বিপুল।
ইসলামপন্থীদের মনে রাখা দরকার, ধর্মবিশ্বাসের মহত্ত্ব আর গভীরতা যেন তাঁদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ওপরও ছাপ রেখে যায়। আসলে, এই দুর্ভাগা দেশের অধিবাসী দুটি সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া শুধু তো জাতীয় স্বার্থের সপ্রতিভ উপলব্ধির ওপর নির্ভর করে না; সত্যদ্রষ্টাদের বাণীনিঃসৃত শাশ্বত প্রেরণার ওপরও তার নির্ভরতা।
সত্য ও শাশ্বতকে যাঁরা জেনেছেন ও জানিয়েছেন, তাঁরা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র। এবং মানুষকেও তাঁরা চিরকাল ভালবেসে এসেছেন।’
এরপর ১৯৩৪ সালের নবীর জন্মদিনে বেতারে সম্প্রচারিত হয়েছিলো কবির লেখা আরেকটি প্রবন্ধ। সেখানে তিনি বলেন:
‘ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের একটি। এই কারণে তার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের সাক্ষ্য দিতে হবে।
ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে, তাদের কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তা সম্ভব হবে না, আমাদের নির্ভর করতে হবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদের অমর জীবন থেকে চির-উৎসারিত।
আজকের এই পুণ্য অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্যে আমার ভক্তি উপহার অর্পণ করে উৎপীড়িত, ভারতবর্ষের জন্য তাঁর আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।’
এরপর দিল্লী জামে মসজিদ থেকে প্রকাশিত The Peshwa পত্রিকার ‘পয়গম্বর’ সংখ্যার জন্য ১৯৩৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতন থেকে কবিগুরু একটা বাণী পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লেখেন:
‘I take this opportunity to offer my veneration to the Holy Prophet Mohammad. One of the greatest personalities born in the world.
Who has brought a new and latent force of life into human history, A vigorous ideal of purity in religion.
And I earnestly pray that those who follow his path will justify their noble faith in their life and the sublime teaching of their master by serving the cause of civilization in building the history of the modern India, helping to maintain peace and mutual good-will in the field of our national life.’
Rabindranath Tagore, Santiniketon, 27 the February 1936
‘যিনি বিশ্বের মহত্তমদের অন্যতম, সেই পবিত্র পয়গম্বর হজরত মহম্মদের উদ্দেশে আমি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।
মানুষের ইতিহাসে এক নতুন, সম্ভাবনাময় জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিলেন পয়গম্বর হজরত, এনেছিলেন নিখাদ, শুদ্ধ ধর্মাচরণের আদর্শ।
সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, পবিত্র পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথ যাঁরা অনুসরণ করছেন, আধুনিক ভারতবর্ষের সুসভ্য ইতিহাস রচনা করে তাঁরা যেন জীবন সম্পর্কে তাঁদের গভীর আস্থা এবং পয়গম্বরের প্রদত্ত শিক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেন।
তাঁরা যেন এমনভাবে ইতিহাসকে গড়ে তোলেন যাতে আমাদের জাতীয় জীবনে শান্তি ও পারস্পরিক শুভেচ্ছার বাতাবরণটি অটুট থেকে যায়।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬
পারস্যের সুফি মুসলিম কবি হাফিজের প্রভাব কবিগুরুর ভেতরে যে প্রকটভাবে ছিলো সেটা সমালোচক মাত্রই স্বীকার করবেন। একটু গভীরে গেলে দেখা যায় শুধু কবিই একলা নন, গোটা ঠাকুরবাড়ি হাফিজে মগ্ন হয়ে থাকতেন।
কবির পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন হাফিজের একনিষ্ঠ ভক্ত। ‘দেওয়ানে হাফিজ’ ছিল ওনার মুখস্ত, কন্ঠস্থ। খুব ভালো ফার্সি জানতেন। আজ আমরা কবিগুরুর যে পোশাক দেখি সেটা কোন ব্রাহ্মণের সাথে না মিললেও মিলে যায় পারস্যের সুফিদের সাথে। এই ঢোলা আলখাল্লার প্রচলন ঠাকুরবাড়িতে করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
হাফিজের প্রভাব ঠাকুরবাড়িতে এমনই প্রবল ছিলো যে, ছেলেদের নিয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন ভোরে উপনিষদ আর হাফিজের গজল গাইতেন বলে শোনা যায়।
এমন অনেক চমকপ্রদ তথ্য দিয়ে রবীন্দ্র গবেষক শেখ সাদী ওনার ‘রবীন্দ্রনাথের সুফিয়ানা’ গ্রন্থে জানান দিচ্ছেন- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মৃত্যুক্ষণেও হাফিজের গজল শুনতে চেয়েছিলেন!
বাঙালী মুসলমানের অবিশ্বাসী মন এখন প্রশ্ন করবে- আচ্ছা মানলাম বাপে অনেক কিছু করছে, তো কি হইছে এতে? আরে ব্যাটা পোলায় কি করছে এইটা বল? রোষো বাবা রোষো। সেখানেই যাচ্ছি আমরা।
‘পারস্য যাত্রী’ নামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা বই আছে। উইকির উন্মুক্ত পাঠাগারে গেলে ফ্রি পড়তে পারবেন।
এই বই পড়লে জানতে পারবেন ৭১ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে কবি ইরাক ও ইরান ভ্রমণে যান। এটাই কবির শেষ বিদেশ ভ্রমণ ছিল। এরপর অবশ্য ১৯৩৪ সালে কবি শ্রীলংকা যান কিন্তু তখনো শ্রীলংকা স্বাধীন হয়নি, তাই সেই ভ্রমণকে নিজের দেশভ্রমণই বলতে হবে। নিজে বর্ণনা করার সময়ও রবিঠাকুর এমনটাই লিখেছেন:
‘দেশ থেকে বেরুবার বয়স গেছে এইটাই স্থির করে বসেছিলুম। এমন সময় পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এলো। মনে হল এ নিমন্ত্রণ অস্বীকার করা অকর্তব্য হবে।’
কোন আবেগে ৭১ বছর বয়সী বৃদ্ধ আর অসুস্থ একটা লোক পারস্যে গেলেন এই অংক যদি ধরতে না পারেন বন্ধু, তাহলে যে লোকটার প্রতি অন্যায় করা হবে!
তো ১৯৩২ সালের ১৮ এপ্রিল হচ্ছে সেইদিন যেদিন হাফিজের সমাধিতে এসে পৌঁছান রবীন্দ্রনাথ। নীরবে কিছুক্ষণ সমাধির সামনে বসেন। সমাধিরক্ষক হাফিজের লেখা বড় আকারের একটি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সামনে নিয়ে আসেন।
সেদেশের মানুষের বিশ্বাস- মনে মনে কোন ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করে বইয়ের পাতা খুললে যে কবিতা বের হবে তা থেকে ইচ্ছার সফলতা নির্ভর করে। তো কবি চোখ বন্ধ করে একটা পাতা খুললেন।
র্যান্ডম একটা বইয়ের পাতা খুললেন কবি। ওই পাতার লেখা তর্জমা করে কবিকে শোনানো হলো।
কবিতাটা এরকম:-‘ মুকুটধারী রাজারা তোমার মনমোহন চক্ষুর দাস, তোমার কণ্ঠ থেকে সুধা নিঃসৃত হয়; জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানেরা তার দ্বারা অভিভূত।
স্বর্গদ্বার যাবে খুলে আর সেইসঙ্গে খুলবে আমাদের সমস্ত জটিল ব্যাপারের গ্রন্থি।’
রবিঠাকুর এই সমাধির সামনে বসেই তার আজন্ম লালিত প্রেম, মহাকবি হাফিজের কবিতা সুর সহ শোনার ইচ্ছে পোষণ করলেন। এইমাত্র পাঠ করা গজলটাই গাওয়া হলো।
ইরানি কবি মুক্তাদেরি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন:
‘কবি এমনভাবে কান পেতে ছিলেন, মনে হচ্ছিলো যেন মোহগ্রস্ত হয়ে গেছেন। সিদ্ধি লাভকারী ধ্যানমগ্ন ঋষির মতো নিমগ্ন রবীন্দ্রনাথের দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।’
জিয়াউদ্দিন বারানীর লেখেন:
‘তাঁর প্রভাবশালী চোখ বেয়ে সাদা দাড়ির ওপর দিয়ে বৃষ্টিধারার মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। গজল শেষে যখন রেজা খান হাতের বেহালা রেখে দিলেন, তখনও রবীন্দ্রনাথ বিলাপ করছিলেন অনেকক্ষণ পর তিনি উঠে বেশ ক’টি দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তার ভেতর এমন আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যা বর্ণনাতীত।’
রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন:
‘আমার সারা জীবনের কবিতা রচনাকালের অবস্থা একপাশে- আর এই কাব্যচিন্তার ক্ষুদ্র মুহূর্তটি এক পাশে। জানি না- এই মাটিতে কী এমন আধ্যাত্মিকতা রয়েছে- যা আমার অন্তরকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।’
পারস্যযাত্রীতে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখছেন:
‘এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে এসে পৌঁছলো, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত।
মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করেছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকদের কুটিল ভ্রূকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক, ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়।
নিশ্চিত মনে হল, আজ কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের চেনা লোক।’
অনেক হলো কবি হাফিজ প্রেমের কথা। অনেকে হয়তো এতোদূর পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ মুসলমানকে শত্রুজ্ঞান করতেন এই কথাটা বলার সময় একটু ধাক্কা খাবেন। উল্টো দিকে অনেক রেফারেন্সপন্থীদের মনে হবে এখনো কম হয়ে গেলো।
আত্মার গল্পে সন্তুষ্টি আমরা আজকাল পাই না। মেশিনগানের মতো চ্যাপ্টার নাম্বার ভার্স নাম্বার বলতে না পারলে কোন তথ্যই সত্য না। চলেন একটু চেষ্টা করি আপনাদের পছন্দের তরিকায়:
রবীন্দ্রনাথের ‘কাবুলিওয়ালা’ গল্পে আছেন মুসলমান রহমৎ খাঁ, ‘দালিয়া’ গল্প উল্লেখ আছেন মুসলমান জুলিখা, আমিনারা। ‘সমস্যা পূরণ’ গল্পে মুসলিম আছিমদ্দির কথা অনেকের মনে আছে, সেখান আছেন আছিমের মা মুসলিম মির্জা বিবি। সেই গল্পের প্লটে মুসলমান ত্রাতার ভূমিকায় আছেন।
একটা একটা করে গল্প দেখলে আরও গোটা বিশেক নাম পাওয়া যাবে।
এভাবে গল্প না দেখে বরং মুসলমান শব্দ সমেত শিরোনাম বা নামগল্প নিয়ে দু’লাইন আলাপ করি।
মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতন থেকে ছাপা ‘ঋতুপত্র‘ পত্রিকায় কবির লেখা ‘মুসলমানির গল্প’ ছাপা হয়। মৃত্যুর আগে কবির এই লেখা উনি শেষ করে যেতে পারেননি, গল্পটি ছিল খসড়া মাত্র।
গল্পে দেখা যায় মাতৃপিতৃহীন কমলার বিয়ে হয়েছে।
এই গল্পের ঘটনাচক্রে একজন হাবির খাঁ’কে দেখবো আমরা, যিনি কমলাকে বলছেন: ‘তুমি আমার কন্যা। তোমার কোনো ভয় নেই। এখন এই বিপদের জায়গা থেকে চল আমাদের ঘরে।’
কমলা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।
হাবির বললেন, ‘বুঝেছি তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে। মুসলমান ঘরে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে। আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে।’
কমলা চলে যায় হাবির খাঁর বাড়িতে। হাবির খাঁ বলেন, ‘তোমার মহলে আমার ছেলেরা কেউ আসবে না। এই বুড়ো ব্রাহ্মণকে দিচ্ছি, এঁকে নিয়ে তোমার পুজো-অর্চনা চলতে পারে।’
গল্পে কমলা মুসলিম হাবির খা’র কাছে যা পায়, তা সে নিজের বাড়িতে কোনোদিন পেতো না। তারপর যৌবনের আবেগ এলো তার দেহে। বাড়ির একটি ছেলে আনাগোনা শুরু করল কমলার মহলে। তার সঙ্গে মনে মন বাঁধা পড়ে গেল। সে হাবিব খাঁকে বলল, ‘বাবা, আমার ধর্ম নেই। আমি যাকে ভালোবাসি, সেই ভাগ্যবানই আমার ধর্ম।’
কমলা বললে, ‘যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন, সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পুজো করি, তিনিই আমার দেবতা। তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি। আমার ধর্মকর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে। তাতে আমার আপত্তি হবে না। আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।’
এর বাইরে আমরা যদি ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পটা দেখি সেখানেও পাবো মুসলমান চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছিলেন গভীর মমতা দিয়ে।
কি মেশিনগানের সাধ মিটেছে? তাহলে আলাপের শেষ কথা কি? শেষ কথা বলতে আসলে কোন কথা নাই।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে কি আরও বেশি মুসলমান ক্যারেক্টার থাকতে পারতো না? অবশ্যই পারতো। সেই সংখ্যানুপাতের বিচার অন্যদিনের আলাপ। বলতে গেলে এক অনিঃশেষ বিতর্কের আলাপের কোন শেষ নাই।
মোটাদাগে প্রশ্ন হচ্ছে ঠাকুর কি মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন? এটার পরিষ্কার উত্তরটা এই লেখায় পাওয়া গেছে।
এখানে উল্লেখিত তথ্যগুলো সত্য হয়ে থাকলে নিশ্চিতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে: ‘না’, উত্তর হচ্ছে: ‘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইসলাম বা মুসলিম বিদ্বেষী ছিলেন না’।
উপনিষদের সাথে সমানতালে হাফিজ পাঠ করে যেই মানুষটার শৈশব কেটেছে, যেই মানুষটা পোশাক হিসেবে বেছে নিয়েছেন সুফিয়ানাকে…
যেই মানুষটা হাফিজের সমাধিতে শিশুর মত কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলেন, তার সমস্ত সাহিত্য এক দিকে আর হাফিজের একটা লাইন একদিকে রাখা হলে হাফিজের লাইনটাই ভারী হবে- সেই মানুষটাকে এতো কুটিল, সন্ত্রাসী, ইসলামফোব হিংস্র মানুষ হিসেবে বধ করা বন্ধ করি আসুন আমরা।
ক্রিটিক্যাল সমালোচনা হোক। আরও কি কি তিনি করতে পারতেন সেইসব আলাপ হোক, রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অবস্থান নিয়ে আলাপ হোক, মুসলমান প্রজাদের তার সাহিত্যে রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে আলাপ হোক, কিন্তু লোকটাকে ইসলামবিদ্বেষী বলাটা বন্ধ করেন ।
‘এই অকুল সংসারে, দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে। ঘোরবিপদ-মাঝে, কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস!’
সংগৃহীত